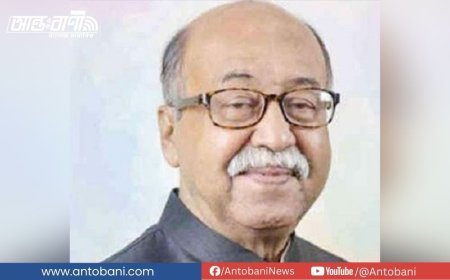আর্গো মিশন: কীভাবে ছয় মার্কিন কূটনীতিক ইরান থেকে পালিয়েছিল!
ইরান বিপ্লবের সময় ৬ মার্কিন কূটনীতিক কীভাবে এক ভুয়া হলিউড সিনেমার আড়ালে তেহরান থেকে পালাতে সক্ষম হয়েছিল? জানুন আর্গো মিশনের এই রোমাঞ্চকর সত্য গল্প। নতুন নতুন ডকুমেন্টারি পেতে সাবস্ক্রাইব করুন আন্তঃবাণী।
৪ নভেম্বর ১৯৭৯।
তেহরানে অবস্থিত মার্কিন দূতাবাসের দেয়াল টপকে হাজার হাজার বিক্ষোভকারী দুতাবাসের ভেতরে ঢুকে পড়েছিল।
তাদের লক্ষ্য ছিল ৫৮ জন মার্কিন নাগরিককে জিম্মি করা।
দূতাবাসের নিরাপত্তারক্ষীরা অবস্থা বেগতিক দেখে অস্ত্র ফেলে দেয়।
কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই ৫২ জন মার্কিন কূটনীতিক এবং কর্মী ইরানি বিক্ষোভকারীদের হাতে বন্দী হয়ে যায়।
তাদের একটাই দাবি ছিল—
“শাহ অফ ইরানকে ফিরিয়ে দাও, না হলে তোমাদের ৫২ জন নাগরিকের মৃতদেহ দেখতে হবে।”
এই বিশৃঙ্খলার মধ্যেই ছয়জন মার্কিন কূটনীতিক গোপন একটি দরজা দিয়ে দূতাবাস থেকে পালাতে সক্ষম হন।
তারা দিন-রাত লুকিয়ে থাকতেন, ছদ্মবেশ ধারন করতেন, কারণ প্রতিদিন তাদের ধরা পড়ার ভয় ধীরে ধীরে আরও বাড়ছিল। তাদের ইরান থেকে জীবিত উদ্ধার করা ছিল একপ্রকার মিশন ইম্পসিবল।
আর এই মিশিন ইম্পসিবল এর দায়িত্ব দেওয়া হয় সিআইএ-কে।
এবং শুরু হয় এক অভিনব পরিকল্পনা— একটি ভুয়া হলিউড সিনেমার শুটিংয়ের গল্প।
যেখানে ছিল ভুয়া অভিনেতা, ভুয়া স্ক্রিপ্ট, এমনকি ভুয়া মুভির পোস্টারও প্রিন্ট করা হয়েছিল।
এটি কোনো বাস্তব সিনেমা ছিল না, এটি ছিল সিআইএ-র একটি গোপন রেসকিউ মিশন। যার কোডনেম ছিল “আর্গো”।
আন্তঃবাণীর আজকের ভিডিওতে আমরা জানাবো এমনই এক সত্যিকারের মিশন ইম্পসিবল এর ঘটনা।
১৯৭৯ সালে ইরানের রাজনৈতিক পরিস্থিতি অস্থির হয়ে উঠেছিল। কয়েক মাস আগে ১৯৭৯ সালের জানুয়ারি মাসে শাহ মোহাম্মদ রেজা পাহলভী, যিনি যুক্তরাষ্ট্র সমর্থিত শাসক ছিলেন, গণবিক্ষোভের চাপে দেশ ছেড়ে পালিয়ে যান। তার ৩৮ বছরের শাসনে আমেরিকার সরাসরি সমর্থন ছিল। কিন্তু ইরানের মানুষ শাহের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল।
কারণ মোহাম্মদ রেজা নিজে আরেম আয়েশের জীবন পার করছিল। রাষ্ট্রে বেশিরভাগ নিয়ন্ত্রন আমেরিকার ছিল। গুরুত্বপূর্ন সকল সিদ্ধান্তই আমেরিকার ইচ্ছানুসারে হতো। তেলকুপগুলোর পুর্ন নিয়ন্ত্রন ছিল আমেরিকার হাতে। অন্যদিকে ইরানের সাধারন জনগন দারিদ্রতার সুচকে দিন দিন নিচের দিকে নেমে যাচ্ছিল। মানুষ বুঝে গিয়েছিল শাহ মোহাম্মদ রেজা আমেরিকার একজন পাপেট মাত্র।
শাহ মোহাম্মদ রেজার সিক্রেট পুলিশবাহিনী ছিল যার নাম ছিল,“সাভাক”। জনগন এই পুলিশের নাম শুনলেই আতংকে থাকতো। কারণ সাভাক যেকোন ধরনের বিরোধি মতকে দমন করতে দক্ষ ছিল।
এই অস্থিরতার মধ্যেই এক ব্যাক্তি দেশে ফিরে আসেন… সে আর কেউ না, আয়াতুল্লাহ রুহুল্লাহ খোমেনি,
সে এক ধর্মীয় নেতা ছিল যার হাতে পুজি ছিল জনগনের ক্ষোভ এবং নিরঙ্কুশ সমর্থন। অল্প সময়ের মাঝেই তিনি ইসলামী বিপ্লবের নেতৃত্ব দিয়ে ইরানকে এক ইসলামী প্রজাতন্ত্রে রূপান্তরিত করেন।
ক্ষমতার পালাবদল এর পরপরই ইরানে মার্কিনবিরোধী মনোভাব তীব্র আকার ধারণ করে। আমেরিকাকে ইরানের জনগন শুধু শাহ মোহাম্মদ রেজার মিত্র হিসেবেই না বরং একটা দুর্নীতিগ্রস্ত পশ্চিমা রাষ্ট্র হিসেবে দেখা শুরু করলো।
তেহরানের রাস্তায় জনসাধারন আমেরিকার বিরুদ্ধে স্লোগান দিতে থাকে, আমেরিকার পতাকা জ্বালাতে থাকে। যখন খবর ছড়িয়ে পড়ে যে যুক্তরাষ্ট্র মোহাম্মদ রেজাকে আশ্রয় দিয়েছে, ইরানিরা রাগে ক্ষোভে ফেটে পড়ে।
তাদের দাবি— মোহাম্মদ রেজাকে ইরানে ফেরত পাঠাতে হবে।
৪ নভেম্বর, হাজার হাজার বিক্ষোভকারী তেহরানের মার্কিন দূতাবাস ঘিরে ফেলে এবং ভেতরে ঢুকে পড়ে।
৫২ জন মার্কিন নাগরিক তাদের হাতে বন্দী হয়।
কিন্তু তারা জানত না, দূতাবাসের পেছনে একটি গোপন দরজা আছে, যা দিয়ে ছয়জন কূটনীতিক পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়।
তাদের নাম ছিল:
রবার্ট অ্যান্ডারস, মার্ক লিজেক, তার স্ত্রী কোরা লিজেক, জোসেফ স্ট্যাফোর্ড, তার স্ত্রী ক্যাথলিন স্ট্যাফোর্ড, এবং লি শ্যটস।
তারা কোথাও লুকোতে পারছিল না। কোনো অফিসিয়াল সাহায্য নিতে পারছিল না। সমগ্র তেহরান তাদের জন্য এক কারাগার হয়ে উঠেছিল।
তাদের সাহায্য করেন একমাত্র কানাডার রাষ্ট্রদূত কেন টেইলর। তিনি তাদের নিজের বাসায় আশ্রয় দেন এবং তিন মাস ছয়জনকে সেখানেই লুকিয়ে থাকতে হয়।
তাদের রক্ষা করা এক চরম ঝুঁকিপূর্ণ বিষয় ছিল। কারণ ইরানি সরকার জানলে কানাডার রাষ্ট্রদুতও মারা যেতে পারত, এবং আটকে থাকা ৫২ জন বন্দীর জীবনও বিপন্ন হতো।
সিআইএ-এর টনি মেন্ডিজ এই মিশনের দায়িত্ব নেন। তাদের উদ্ধার করতে তিনি এক অভিনব পরিকল্পনা তৈরি করেন—
একটি ভুয়া সায়েন্স ফিকশন সিনেমার শুটিংয়ের আড়ালে তাদের বের করে আনার পরিকল্পনা।
এর জন্য হলিউডে একটি আসল অফিস খোলা হয়, পোস্টার ছাপানো হয়, ভুয়া স্ক্রিপ্ট লেখা হয়। মিডিয়ায় সিনেমার খবর ফাঁস করা হয়, ভুয়া ইন্টারভিউ প্রকাশ করা হয়।
জানুয়ারি ১৯৮০-তে টনি মেন্ডিজ তেহরানে পৌঁছান। কানাডার সিনেমার প্রযোজক হিসেবে তার বৈধ পাসপোর্ট ও নথি ছিল তার সাথেই। তেহরানে পৌঁছে তিনি গোপনে ছয়জনের সাথে দেখা করেন এবং এয়ারপোর্টে কীভাবে আচরণ করতে হবে তা শিখিয়ে দেন।
প্রতিটি কূটনীতিককে সিনেমার ক্রু হিসেবে আলাদা পরিচয় দেওয়া হয়— কেউ রাইটার, কেউ সিনেমাটোগ্রাফার, কেউ প্রোডাকশন ডিজাইনার। তাদের হাতে দেওয়া হয় কানাডিয়ান ভুয়া পাসপোর্ট এবং প্রয়োজনীয় ডকুমেন্ট।
তাদের শিখানো হয় কীভাবে কাস্টম অফিসারদের সামনে কনফিডেন্ট নিয়ে কথা বলতে হবে। তাদের পুরোপুরি সিনেমার ক্রুতে রূপান্তরিত করা হয়।
অবশেষে আসে সেই দিনটি।
ছয়জন কুটনৈতিক সহ পুরো ভুয়া সিনেমার টিমটি তেহরান এয়ারপোর্টে পৌঁছায়। তাদের আচার-আচরণ ছিল একদম স্বাভাবিক, আত্মবিশ্বাসী। তাদের ভুয়া পাসপোর্টে ইরান এন্ট্রির স্ট্যাম্প না থাকলেও, তাদের আত্মবিশ্বাস এবং কানাডার দূতাবাসের সমর্থনে তারা পার পেয়ে যায়। কারণ ক্ষমতার পালাবদলে এন্ট্রি স্ট্যাম্প ছাড়া ইরানে ঢুকে পড়া ছিল তখনকার সময়ে স্বাভাবিক ঘটনা। তারা স্বাভাবিকভাবে বোর্ডিং করে, প্লেনে উঠে বসে। ইরানের আকাশসীমা ছাড়ার পর তারা বুঝতে পারে, তারা সত্যিই বেঁচে গেছে।
তাদের চুপিসারে সুইজারল্যান্ড হয়ে যুক্তরাষ্ট্রে নিয়ে যাওয়া হয়। মিডিয়া এই ব্যাপারে কোনো খবর প্রকাশ করে না।
সবকিছু গোপন রাখা হয়। ১৭ বছর পর, ১৯৯৭ সালে সিআইএ এই মিশনের নথি প্রকাশ করে। তখন সারা বিশ্ব জানে, কীভাবে এক ভুয়া সিনেমার আড়ালে ছয়জন কূটনীতিককে বাঁচানো হয়েছিল।
এই গল্পের উপর ভিত্তি করে পরবর্তীতে “আর্গো” নামে একটি সিনেমাও তৈরি হয়। যদিও সিনেমায় সিআইএ-র ভূমিকা বড় করে দেখানো হয়, বাস্তবে কানাডার রাষ্ট্রদূত কেন টেইলারের অবদান ছাড়া এই মিশন সম্ভব ছিল না।
কেন টেইলরকে কানাডায় জাতীয় নায়ক ঘোষণা করা হয়, এবং যুক্তরাষ্ট্র তাকে কৃতজ্ঞতা স্বরুপ স্বর্ণপদক দেয়।
আর্গো মিশনের পর ইরানে মার্কিন দূতাবাস আর কখনোই খোলা হয়নি। কানাডাও তার দূতাবাস বন্ধ করে কূটনীতিকদের ফিরিয়ে আনে। অনির্ধিষ্টকালের জন্য সম্পর্ক নষ্ট হয়ে যায় ইরান এবং আমেরিকার।